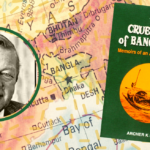ভাষা ও জিন – আলী আফজাল খান
আশির দশকের শেষের দিকে পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত এক ব্রিটিশ পরিবারের সদস্যদের (KE Family) মধ্যে সর্বপ্রথম ভাষাগত সক্ষমতার সমস্যা চিহ্নিত করা হয়। পরিবারটির সন্তান-সন্ততিরা Elizabeth Augur-এর পশ্চিম লন্ডনের বিশেষায়িত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ার সময় সমস্যাটি ধরা পড়ে। অনুসন্ধানে বের হয়ে আসে যে, পরিবারটির কথা বলার সমস্যা তিন প্রজন্মে বিদ্যমান এবং ৩০ জন সদস্যের মধ্যে ১৬ জনই ঠিক মতো ভাষা ব্যবহার করতে পারে না। পরিবারটির সদস্যদের মধ্যে কারও সমস্যাটি কম, কারও গুরুতর, আবার কারও একদম নেই। আক্রান্তরা উচ্চারণ সম্পূর্ণ করতে পারত না, সীমিত শব্দ ভাণ্ডার, বিশেষত ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণ করতে পারত না। ১৯৯০ সালে বিজ্ঞানীMarcus Prembey and Jane Hurst পরিবারটির নমুনা বিশ্লেষণ করে গবেষণার মাধ্যমে সমস্যাটি বংশগত বা জিনগত সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেন। ২০০১ সালে Faraneh Vargha-Khadem যে জিনটি ভাষা সক্ষমতা তৈরি এবং উৎকর্ষতায় জড়িত সেটা আবিষ্কার করেন এবং নাম দেন FOXP2 (FORKHEAD BOX P2),, মানুষের অনন্য বৈশিষ্ট্য ভাষার ব্যবহারের জন্য দায়ী ‘ভাষা জিন’ (language Gene) FOXP2 আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে এক নতুন দিগন্ত উন্মেচিত হয়। বিবর্তনের ধারায় প্রায় ৫০ হাজার বছর আগে মানুষের এই জিনে এমন মিউটেশন হয় যাতে মানুষ ভাষা ব্যবহারের অনন্য সক্ষমতা অর্জন করে।১
পরবর্তীতে গবেষণায় দেখা যায়, বস্তুত শুধুমাত্র একটি জিন মানুষের ভাষা সক্ষমতা সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে না এবং বৈজ্ঞানিকভাবে এটি প্রমাণিত যে, কয়েকটি জিন সমষ্টি মানুষের ভাষা সক্ষমতা তৈরিতে ভূমিকা রাখে। কিন্তু এটাও সত্য FOXP2 জিন মানুষকে অন্যান্য প্রানিগোষ্ঠী থেকে ভাষাগত দিক দিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন উন্নত প্রাণী হিসেব দাঁড় করিয়েছে। এই বিশেষ জিনটি যদিও মানুষসহ অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণী যেমন শিম্পাঞ্জী, পাখি ইত্যাদির মধ্যে বিদ্যমান, কিন্তু চমৎকার বিষয় হচ্ছে মানুষের FOXP2 জিনে কমপক্ষে দুটি জায়গায় (এমিনো এসিড) ভিন্নতা আছে, এই মিউটেশন শুধু মানুষের ক্ষেত্রেই হয়েছে, যার ফলে জিনটি মস্তিষ্কের ৬৫টির বেশি জায়গা প্রভাবিত করে। ফলে মস্তিষ্কে যোগাযোগের উন্নত ব্যবস্থা ভাষা সক্ষমতা তৈরি হয়েছে মানুষের।২
ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের FOXP2 এর প্রকাশ বেশি যে কারণে দেখা যায় মেয়ে শিশুদের ছেলে শিশুর তুলনায় ভাষাগত দক্ষতা বেশি। FOXP2 জিন যে জিনটিকে প্রভাবিত করে সেটিও বৈজ্ঞানিকরা আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছেন, জিনটির নাম SRPX2|3
Humans have a unique natural ability to develop highly complex linguistic systems- an ability that lies in our genes but is also shaped by our different environments. We can learn languages from others and use them to share our thoughts, feelings and desires; languages are the foundation of society, culture and science. What is so special about our genetic make-up that allows us to use language? How does the ability relate other higher cognitive functions like human memory and mathematical or musical ability?
জিন শব্দটা শুনলেই মনের অজান্তেই আমাদের মনে এক অজানা রহস্যের সৃষ্টি হয়। মনে হয় শৈশবকালের দাদা দাদির কাছে গা ছমছম কথা, ডানা কাটা পরী ও জিনের গল্প। আমাদের বর্তমান আলোচনার জিন আর শৈশবের রহস্যময় জগতে বা বিশ্বাসের পরাজগতের জিন এক নয়।
যখন কোনো নবজাতক গগন বিদারি চিৎকারে ভূমিষ্ঠ হয় তখন থেকেই আমরা ব্যস্ত থাকি নবজাতকটি কার মতো হয়েছে, কেউ হয়ত নবজাতকের নাকের সাথে মায়ের নাকের সাদৃশ্য খুঁজে পায়, আবার কেউ নবজাতকের চোখের সাথে বাবার মিল খোঁজে। কেউ হয়তো অবয়ব বিশ্লেষণে নবজাতকের গায়ের রং বা গঠনে খুঁজে পায় দাদা দাদি বা নানা নানির মিল।
আমরা অনেক সময় শুনে থাকি তোমার এই প্রাণ খোলা হাসিটা ঠিক তোমার বাবার মতো। আবার এইও শুনি তোমার বাবা শৈশবকালে ঠিক তোমার মতো দূরন্ত ছিল। অর্থাৎ গঠন অবয়ব বা বৈশিষ্ট্য বংশানুক্রমে প্রবাহিত হয়। আর এটাই বংশগতি, আমরা আমাদের বৈশিষ্ট্য পেয়েছি আমাদের মা-বাবার কাছ থেকে, আবার আমাদের মা-বাবারা পেয়েছে তাদের মা বাবার কাছ থেকে। বৈশিষ্ট্যের যে প্রবাহ তা আসলে জিনেরই প্রবাহ। অর্থাৎ জিন প্রবাহিত হয় মা-বাবা থেকে সন্তান-সন্ততিতে। জিন আসলে একটা বৈশিষ্ট্য কোড করে। একটি ইমারতের গঠন একক যদি ইট হয় তবে আমাদের দেহের ইট হচ্ছে কোষ। অর্থাৎ আমরা হচ্ছি আমাদের দেহ কোষের সমষ্টি। আমাদের দেহকোষের সব কার্যকলাপের সমষ্টি হচ্ছে আমাদের এক একজনের কার্যকলাপ। অর্থাৎ আমাদের জীবন হচ্ছে আমাদের দেহকোষের সব প্রাণরাসায়নিক বিক্রিয়ার মূল।
আমাদের দেহ কোষের আকার দেহের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম। চোখের কোষ এক রকম আবার কিডনি বা হৃদযন্ত্রের কোষ অন্য রকম। কোষের নিজস্ব আভ্যন্তরীন গঠন বিন্যাস আছে। কোষকে আমরা এভাবে কল্পনা করতে পারি, থকথকে কিছু জেলির ন্যায় পদার্থ পর্দা দ্বারা আবৃত। জেলির মধ্যে একটি গোলাকার বস্তু ভাসমান যাকে আমরা নিউক্লিয়াস বলি। যদি কোষকে ডিমের সাথে তুলনা করি তাহলে কুসুম হচ্ছে নিউক্লিয়াস। আসলে ডিমও এক প্রকার কোষ। এই নিউক্লিয়াসের ভিতর প্যাঁচানো কিছু সুতো থাকে যাকে ক্রোমোসোম বলে। ক্রোমোসোম হচ্ছে ডিএনএ নামক সুুুুুতা, প্রোটিন আবরণ দিয়ে প্যাঁচানো থাকে। অর্থাৎ ক্রোমোসোম থেকে প্রোটিন সরিয়ে নিলে যা থাকে তাই হচ্ছে ডিএনএ।
আমাদের প্রাণরাসায়নিক বিক্রিয়া পরিচালিত হয় এনজাইমের মাধ্যমে, আর এনজাইম হচ্ছে প্রোটিন। আমরা যে খাবার খাই, তা বিভিন্ন ধরনের এনজাইমের মাধ্যমে বিপাক হয়। আমাদের যে চামড়ার রং তাও এক ধরনের প্রোটিনের কারণে। গায়ের রং মেটা মেলানিন নামক রঞ্জক প্রোটিনের কারণে। মেলানিনের আধিক্য বেশি হলে গায়ের রং কালো হয়। আবার মেলানিন কম থাকলে গায়ের রং ফর্সা হয়। অর্থাৎ আমাদের শারীরবত্তীয় কার্যকলাপ নির্ধারিত হয় প্রায় দুই লাখের মতো প্রোটিন দ্বারা।
জিন হচ্ছে ডিএনএ এর একটি অ ল যা একটি নির্দিষ্ট প্রোটিনকে কোড করে। অর্থাৎ আমাদের শারীরবৃত্তীয় কার্যকলাপ জিনের মধ্যে কোড করা থাকে। ডিএনএ আবার চার ধরনের ইট দিয়ে গঠিত। এই ইটগুলোকে নিউক্লিওটাইট বলে; এডিনিন, গুয়ানিন, থাইমিন এবং সাইটোসিন। এদের ক্রমবিন্যাস হচ্ছে জেনেটিক কোড। মানুষে মানুষে জেনেটিক কোডের যেমন সাদৃশ্য আছে তেমনি বৈসাদৃশ্যও আছে। তাইতো কারও চোখ কালো আবার কারও চোখ নীলাভ। কারও কন্ঠ সুরেলা আবার কারও কন্ঠ কর্কশ।
জাতিগতভাবেও জিনের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আছে। যেমন চীন বা জাপানের লোকদের দৈহিক অবয়ব আর বাঙালিদের অবয়ব এক নয়। দুটি জাতির জেনেটিক সাদৃশ্য যদি বেশি থাকে তবে তাদের দেহ অবয়ব বা আচার আচরণের মিল বেশি থাকে। জেনেটিক সাদৃশ্যতা দিয়ে একটি জাতির আদি পুরুষ কোথা থেকে এসেছে তা বোঝা যায়। অর্থাৎ কোনো জাতির মাইগ্রেশন প্যাটার্ন বোঝা যায়।
যদি ধরে নেয়া হয় সৃষ্টির আদিতে মানুষের জিন একরকম ছিল তাহলে সময়ের সাথে জিনগুলো ক্রমবর্ধমান বিবর্তনের বা পরিবর্তনের কারণেই মানুষে মানুষে বা জাতিতে জাতিতে এত বৈচিত্র্যতা।
টোনের (Tone) উপর ভিত্তি করে ভাষাকে ভাগ করা যায়। প্রত্যেক ভাষাতেই স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জণবর্ণ ব্যবহার করা হয় এবং শব্দ থেকে অন্য শব্দকে পৃথক করার জন্য টোনযুক্ত ভাষা যেমন চৈনিক ভাষা পিচ (Pitch) ব্যবহৃত হয় শব্দের শেষে, অন্যদিকে টোনবিহীন ভাষায় পিচ (যেমন ইংরেজি) ব্যবহৃত বাক্যের শেষে। পিচ বা ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার করা হয় আবেগ ও গুরুত্ব বোঝানোর জন্য। সাব সাহারা অ লের ভাষা টোনযুক্ত, অন্যদিকে ইউরেশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার ভাষা টোনবিহীন। বিজ্ঞানীরা (Tone) টোনযুক্ত ও টোনবিহীন ভাষার সাথে জিনের সম্পর্ক দেখিয়েছেন। এক্ষেত্রে তারা দৃষ্টি দিয়েছেন মস্তিষ্কের গঠনের বৃদ্ধি ও উৎকর্ষের (Growth and development) সাথে জড়িত দুটি জিন। জিন দুটি হচ্ছে ASPM Ges Microcephalin|
।
আমাদের মানব কোষে প্রত্যেকটি জিন জোড়ায় জোড়ায় থাকে। একটি আসে বাবার কাছ থেকে অন্যটি আসে মায়ের কাছ থেকে। জোড়া জিন দুটির মধ্যে কিছুটা পার্থক্য থাকতে পারে এবং এদেরকে আলাদাভাবে ঐ জিনের Allele বলে। অর্থাৎ সাধারণভাবে কোনো জিনের অষষবষব দুটি। কিন্তু যখন বিস্তৃত জনসংখ্যার সাথে তুলনা করা হয় তখন ঐ জনগোষ্ঠীর কোনো জিনের অনেক Allele থাকতে পারে। কোনো জিনের ভিন্নরূপকেই Allele বলা হয় ।
কোনো একটি নির্দিষ্ট Allele এর ফ্রিকোয়েন্সি একক জনগোষ্ঠীতে একেক রকম। ধরা যাক কোন জিনের ‘ক’ নামক Allele এর ফ্রিকোয়েন্সি বাঙালি জাতীতে ৭০% তা হয়তো চীনা জাতিতে ৩০%, Allele ফ্রিকোয়েন্সি বিশ্লেষণ করেও জাতিগত সাদৃশ্য তুলনা করা হয়। ASPM জিন এর একটি Alleleহচ্ছে ASPM-D, অন্যদিকে Microcephalin (MCPH 1) এর একটি Allele MCPH-D, এই দুটি Allele Gi এর ফ্রিকোয়েন্সি বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, টিউনবিহীন ভাষার জাতিতে এদের ফ্রিকোয়েন্সি বেশি। অন্যদের টিউন ভাষাতে এ জিন দুটির ফ্রিকোয়েন্সি কম।৪
মানুষের ভাষার বিকাশ ঘটেছে তিনটি ধাপে। প্রথমত; ধ্বনিগত ও দেহভাষার স্তর, যে স্তরে মানুষ কিছু সীমিত ধ্বনি আর অঙ্গভঙ্গি দিয়ে অর্থ বিনিময় করেছে। দ্বিতীয়ত; শব্দমূলগত স্তর, যে স্তরে মানুষ যৌগিক ধ্বনির বিন্যাস দিয়ে অনেক শব্দ তৈরি করে, সেগুলোর অর্থ নিষ্পত্তি করে ব্যবহার করা শুরু করেছে বার্তা আদান-প্রদানের জন্য। তৃতীয়ত; বাক্য স্তর যেখানে মানুষ শব্দগুলো জটিল ব্যাকরণিক সূত্র দিয়ে গাঁথবার মধ্য দিয়ে আরও জটিল ভাব আদান-প্রদানের সামর্থ্য অর্জন করেছে। বিবর্তনবাদী আলোচনায় বাক্যের চেয়ে শব্দের প্রতি বেশি মনোযোগ দেয়া হয়। পরবর্তীতে কাঠামোবাদী ভাষাবিজ্ঞান সেই ঘাটতি পুষিয়ে দিয়েছে। বিবর্তনবাদীদের অনুমান, এই সবকিছুই ঘটতে সময় লেগেছে প্রায় ১০ লাখ বছর। বিবর্তনের সূত্রে সময়কালের যে ধারণা তাতে এটা মনে হয় খুব বেশি সময় নয়। ভাষা বৈচিত্রকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রেও বিবর্তনবাদী ধারায় বহু আলোচনা রয়েছে। এই প্রশ্নে মানুষের উৎসমূল আর ভাষার উৎসমূলের আলোচনা প্রায় একই রকম। এখানে মৌলিক দুটি ধারণার একটি হচ্ছে পৃথিবীর ভাষাগুলো বিভিন্ন জায়গায় স্বতন্ত্রভাবে বিকশিত হয়েছে। অন্যটি হচ্ছে একটি অভিন্ন ভাষা থেকে পৃথিবীর সব ভাষার উদ্ভব ঘটেছে। এই দুই অনুমানেই ভাষার জায়গায় মানবজাতি বসিয়ে নিলেও আলোচনার ছকের খুব একটা হেরফের হয়না।৫
গত একশত প াশ বছর যাবৎ ভাষাবিদরা ভাষার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে পৃথিবীর সব ভাষাকে কয়েকটি ভাষা বর্গে বা পরিবারে ভাগ করেছে। পণ্ডিতগণ একই পরিবারের শ্রেণীসমূহ থেকে কিছু মৌলিক শব্দ তুলনা করে শ্রেণীসমূহের সম্পর্ক নিরূপণ করেছেন। বেশির ভাগ ভাষাই কোনো না কোনো ভাষা পরিবারের অন্তর্গত। বিশ্বে প্রায় ১০০টিরও বেশি ভাষা পরিবার বিদ্যমান।৬
উলেখযোগ্য ভাষা পরিবারগুলি হচ্ছে:
১ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পরিবার
২ উরালীয় ভাষা পরিবার
৩ আলতায়ীয় ভাষা পরিবার
৪ চীনা-তিব্বতি ভাষা পরিবার
৫ মালয়-পলিনেশীয় ভাষা পরিবার
৬ আফ্রো-এশীয় ভাষা পরিবার
৭ ককেশীয় ভাষা পরিবার
৮ দ্রাবিড় ভাষা পরিবার
৯ অস্ট্রো-এশীয় ভাষা পরিবার
১০ নাইজার-কঙ্গো ভাষা পরিবার
ইন্দো-ইউরোপিয়ান বর্গে মধ্যে ইউরোপের প্রায় সব দেশের এবং ভারত, বাংলাদেশ, ইরান ও আফগানিস্তানের ভাষা অন্তর্ভুক্ত। প্রায় দুইশত জীবিত ভাষা এই বর্গের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের বাংলা ভাষা ইন্দো-ইউরোপিয়ান ভাষা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। এই ভাষা পরিবারটির অন্তর্গত ভাষাতেই পৃথিবীর সর্বাধিক মানুষ কথা বলে এবং এই ভাষা পরিবারের উপরেই সবচেয়ে বেশি গবেষণা হয়েছে। বাংলা ছাড়া এই ভাষা পরিবারের অন্তর্গত ভাষাগুলোর মধ্যে আছে ইংরেজি ভাষা, স্পেনীয় ভাষা, পর্তুগিজ ভাষা, ফরাসি ভাষা, ইতালীয় ভাষা, জার্মান ভাষা, সুয়েডীয় ভাষা, রুশ ভাষা, গ্রিক ভাষা, ফার্সি ভাষা, পশ্তু ভাষা, উর্দু ভাষা, সিন্ধি ভাষা, হিন্দি ভাষা, গুজরাটি ভাষা, পাঞ্জাবি ভাষা, মারাঠি ভাষা, ওড়িয়া ভাষা, অসমীয়া ভাষা। এছাড়াও আছে ধ্র“পদী ভাষা যেমন সংস্কৃত ভাষা, লাতিন ভাষা ও আদি পারসিক ভাষা।
ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলোকে চারটি প্রধান শাখায় ভাগ করা যায় :
ক. ইন্দো-ইরানীয় ভাষাসমূহ
খ. রোমান্স ভাষাসমূহ
গ. জার্মানীয় ভাষাসমূহ
ঘ. বাল্টো-স্লাভীয় ভাষাসমূহ
যে আদি ভাষা থেকে বাংলা ভাষার উৎপত্তি তা অন্তত তিনহাজার বছরের পুরনো। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের একটি হলো ভারতীয় আর্যভাষা। ঋগে¦দের মন্ত্রে যে আর্যভাষা পাওয়া যায় তার নাম প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা, যা লিখিত হয়েছিল যিশুখ্রিস্টের জন্মেরও এক হাজার বছর আগে। বেদের শ্লোকগুলোকে তার অনুসারীরা পবিত্র ভেবে মুখস্থ করে রাখত; ফলে সেগুলো থেকে যায় প্রায় অবিকৃত, কিন্তু অন্যদিকে সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা বদলে যেতে থাকে। ফলে সাধারণ মানুষের কাছে একসময় বৈদিক ভাষা দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। সে সময়ে ব্যাকরণবিদরা, বিশেষ করে পাণিনির মতো জগদ্বিখ্যাত ব্যাকরণবিদ, নানা নিয়ম বিধিবদ্ধ করে একটি মানসম্পন্ন ভাষা সৃষ্টি করেন, যার নাম ‘সংস্কৃত’। ‘সংস্কৃত’ শব্দটির অর্থই হলো পরিশীলিত বা বিধিবদ্ধ। বাংলায় প্রচুর সংস্কৃত শব্দের উপস্থিতি দেখে আগে ধারণা করা হতো বাংলা বুঝি সংস্কৃত থেকেই উদ্ভূত বা এর কন্যা। সংস্কৃত ছিল সমাজের উঁচুশ্রেণীর মানুষের লেখার ভাষা, আড়ম্বরপূর্ণ এবং নিয়মের নিগড়ে বাঁধা। এ ভাষায় মানুষ কথা বলত না, মানুষ কথা বলত কথ্য ভাষায়Ñযার নাম ‘প্রাকৃত’। এই প্রাকৃত ভাষা থেকেই উদ্ভব ঘটেছে বাংলার। সে সময়ে অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব ৪৫০ অব্দ থেকে ১০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন অ লের মানুষ বিভিন্ন ‘প্রাকৃত’ ভাষায় কথা বলত। ভাষাতত্তবিদ জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসনের মতে, বাংলার উদ্ভব হয়েছে মাগধী প্রাকৃত থেকে। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মত কিছুটা ভিন্ন। তাঁর মতে, বাংলার উৎপত্তি ঠিক মাগধী থেকে নয়, বরং এর অপভ্রংশ থেকে, যার নাম মাগধী অপভ্রংশ। ড. মুহম্মদ শহীদুলহ অবশ্য মনে করেন বাংলা যে প্রাকৃত থেকে উদ্ভূত হয়েছে তার নাম গৌড়ি প্রাকৃত। তিন ভাষাপণ্ডিতই যে বিষয়ে একমত তা হল সংস্কৃত নয়, বাংলার আদি জননী হলো প্রাকৃত।৭
জেনেটিক ট্রি এবং ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রি৮ তুলনা করলে দেখা যায়, একই ভাষাভাষি জনগোষ্ঠীর মধ্যে জিনগত সাদৃশ্য উচ্চমাত্রার। সাধারণভাবে তাই ধরে নেয়া যায় যে, একই ভাষাভাষি জনগোষ্ঠীর ভাষা ও জিনের বিবর্তনের কালিক ইতিহাস অভিন্ন। যদিও ইতিহাসের বিশাল কালখণ্ডে কিছু কারণ প্রভাবিত করেছে ব্যতিক্রম তৈরিতে, এই ভিন্নতার কারণ হতে পারে দুইভাবে:
১. ভাষা প্রতিস্থাপন (Language Replacement):
অনাবাসী ও অল্প জনবহুল কোনো এলাকায় দ্রুত বর্ধনশীল কোনো জনগোষ্ঠীর অধিগ্রহণে ভাষা প্রতিস্থাপন হতে পারে। যেমন ঘটেছে নিউ গায়েনা, অস্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকার ক্ষেত্রে। ব্যাপক হারে অভিবাসী বসতি স্থাপনে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভাষা তাসমেনিয়া এবং ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জ হতে সম্পূর্ণ হারিয়ে গেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবশ্য অভিবাসনের পরও আদিবাসীরা তাদের ভাষাটি বাঁচিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছেন।(Basques, Lapps, Eskimas, Khoisam) এক্ষেত্রে অবশ্য প্রাগৈতিহাসিক সময়ে জনবসতির অভিবাসন ছিল কৃষি ব্যবস্থাপনার বিস্তারের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এবং শান্তিপূর্ণ। যদিও আদিবাসী, অভিবাসীদের মধ্যে আন্তঃবিবাহ সম্পর্কের কারণে ভাষা ও গড় জিনোটাইপের কিছু পার্থক্য তৈরি হয়েছে।
২. জিন প্রতিস্থাপন: (Gene Replacement):
প্রতিবেশী জনগোষ্ঠীর ধারবাহিক gene প্রবাহের কারণেই জিন প্রতিস্থাপন ঘটে। জিন প্রতিস্থাপনের আদর্শ দৃষ্টান্ত হচ্ছে আফ্রিকান/ব্লাক আমেরিকানরা। পূর্ব পুরুষদের তুলনায় ব্লাক আমেরিকানদের গায়ের রং উজ্জ্বল হয়। জিন বিশ্লেষণে দেখা গেছে, আফ্রিকানদের গড়ে ৩০% জিন পোল ইউরোপিয়ান থেকে, এক্ষেত্রে (শ্বেত আমেরিকান) জিন থেকে এসেছে আংশিক প্রতিস্থাপন ঘটেছে গত ৩০০ বছরে। এই হারে জিন প্রতিস্থাপন ঘটতে থাকলে আগামী ২০০০ বছরে আফ্রিকান আমেরিকানদের জিন পুলে পূর্বপুরুষদের জিন থাকবে মাত্র ৯%।

চিত্র: ভাষা পরিবার।৯

চিত্র: Phylogenetic tree.10
Figure: Map of Bangladesh showing the sampling area and suggested geneflow from different directions.
বাংলাদেশে বসবাসরত উপজাতিগুলোর মধ্যে চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা জাতির (এদের বর্তমানে ব্যবহৃত ভাষা তিব্বতো-বার্মা ভাষা পরিবারের অন্তর্ভ্ক্তু, ধারণা করা হয় ভাষা পরিবারটি চীন থেকে জন্ম নিয়ে বার্মা এবং বৃহত্তর হিমালয় অ লে বিস্তার লাভ করে) জিন বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, বাংলাদেশের তিব্বতো-বার্মা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর স্বাসে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, পূর্ব এশিয়া এবং ভারতের তিব্বতো-বার্মা ভাষাভাষি জনগোষ্ঠীর সাথে জিনগত বহন করছে এবং ভাষাগত জাতীয়তা রয়েছে।১
কোনো জাতির জিনগত বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা হয় উচ্চতর বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মাইটোকন্ড্রিয়াল উঘঅ (মাতৃতান্ত্রিক বিশ্লেষণ) এবং ওয়াই (পিতৃতান্ত্রিক বিশ্লেষণ) ক্রোমোসোম বিশ্লেষণ করে। বাংলাদেশের ডিএনএ ল্যাবের বৈজ্ঞানিকগণ পপুলেশন জেনেটিক বিজ্ঞানী প্রফেসর শরীফ আক্তারুজ্জামানের নেতৃত্বে (National forensic DNA profiling Laboratory) বাঙালি জাতির ওয়াই (Y) ক্রোমোসোম নিয়ে গবেষণা করেছেন এবং অন্যান্য জাতীর ওয়াই ক্রোমোসোমের সাথে (তখন পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যের) বাঙালী জাতির একটা তুলনামূলক গবেষণা দেখিয়েছেন। সেই গবেষণায় দেখা যায়, তিব্বতসিনো ভাষা গোষ্ঠীর যেমন চায়না, কোরিয়ান, জাপান এদের জেনেটিক সাদৃশ্যতা অন্য ভাষা গোষ্ঠীর তুলনায় অনেক বেশি।১২ আবার বাংলা ভাষী জনসংখ্যার জেনেটিক সাদৃশ্যতা ইন্দো-ইউরোপীয়ান ভাষা গোষ্ঠীর জাতির সাথে মিল বেশি। দেখা গেছে ওয়াই ক্রমোসোমের ক্ষেত্রে বাঙালি জাতির সাথে ভারতীয় দক্ষিণের তামিল জাতি, পাঞ্জাবি জাতির এবং গাদ্দি১৩ (দ্রাবিড় ভাষা, পরিবারের অন্তর্ভুক্ত) উপজাতির সাথে মিল বেশি। কে জানে হয়তো তামিল, পাঞ্জাবী ও বাঙালীর আদি পুরুষ একই। হয়ত বাঙালিদের মাইগ্রেশন দক্ষিণ ভারতের তামিল অথবা পাঞ্জাব থেকেই হয়েছে অথবা তামিলদের মাইগ্রেশন বাংলাদেশ থেকে হয়েছে। আমরা ইতিমধ্যে জানি, বাংলা ভাষার মতো পাঞ্জাবি ভাষাও ইন্দো ইউরোপিয়ান ভাষা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। ভাষাবিদরা হয়তো ভবিষ্যতে গবেষণা করবেন বাংলা ও তামিল এবং বাংলা ও গাদ্দি ভাষার সাথে কতটা মিল রয়েছে। তামিল ভাষা দ্রাবিরিয়ান ভাষা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। বাংলা যেহেতু প্রকৃত ভাষা থেকে জন্ম নেয়া ভাষা, খুব সম্ভব যে দ্রাবিড় ভাষা পরিবারের সাথেও বাংলার শিকড় ছড়িয়ে আছে।
দ্রাবিড় ভাষাসমূহ দক্ষিণ এশিয়ার প্রচলিত ৭৩টি ভাষার একটি পরিবার। এই ভাষাগুলোতে প্রায় ২২ কোটি লোক কথা বলেন। তেলুগু, তামিল, কন্নড় ও মালয়লম চারটি প্রধান দ্রাবিড় ভাষা। বাকি ভাষাগুলোর মধ্যে গোন্ডি, তুলু, কুরুখ উলেখযোগ্য।
দ্রাবিড় ভাষাগুলো মূলত ভারতের দক্ষিণ, পূর্ব ও মধ্য অ লে প্রচলিত। ভারতের বাইরে শ্রীলংকাতে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, প্রশান্ত মহাসাগর, পূর্ব আফ্রিকা ও অন্যান্য প্রবাসী দ্রাবিড় স¤প্রদায়েও এগুলি প্রচলিত। দ্রাবিড় ভাষাগুলোর মূল অ ল থেকে অনেক দূরে পাকিস্তানে ব্রাহুই নামের দ্রাবিড় ভাষাটিতে প্রায় সাড়ে ৭ লাখ লোক কথা বলেন।
চিত্র: দ্রাবিড় ভাষাসমূহের বিস্তার।
তামিল অত্যন্ত প্রাচীন একটি ভাষা। খ্রিস্টপূর্ব ৩য় শতকে এতে রচিত সাহিত্যের নিদর্শন পাওয়া গেছে। দ্রাবিড় ভাষাগুলোর মধ্যে তামিলের সাহিত্যই সবচেয়ে প্রাচীন এবং এটি অনেকটা সংস্কৃতের সমতুল্য। ব্রাহ্মণ ও অ-ব্রাহ্মণদের বলা তামিল ভাষার মধ্যে পার্থক্য আছে, অর্থাৎ তামিল ভাষা কেবল ভৌগোলিকভাবেই নয়, সামাজিক মর্যাদা অনুযায়ীও ভিন্ন হতে পারে। এছাড়া আনুষ্ঠানিক তামিল ভাষা ও কথ্য তামিল ভাষার মধ্যেও বড় পার্থক্য বিদ্যমান।
দ্রাবিড় ভাষার প্রভাব বাংলা ভাষায় পড়েছে, পন্ডিতেরা আমাদের শব্দভান্ডারে দ্রাবিড় ভাষা থেকে আগত বেশ কিছু শব্দ এবং বাক্যগঠন রীতিতে দ্রাবিড় ভাষার প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। তবে তা কতটুকু সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে আর কতটুকু সরাসরি দ্রাবিড় ভাষা থেকে প্রাপ্ত, তা এখনও গবেষণার বিষয় বস্তু। সুনীতকুমার চট্টোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে বাংলা ভাষার গঠন, বাক্যরীতি, উচ্চারণ ও শব্দ ভান্ডারে অবশ্য দ্রাবিড় প্রভাব আছে, কিন্তু এই ধরনের ঐক্য কেবল বাংলা ভাষাতেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং সকল নব্য ভারতীয় আর্য ভাষায় রয়েছে।
বাংলা ভাষায় অস্ট্রিক ভাষার উপাদানের অস্তিত্বও অনুরুপভাবে প্রমাণ করে যে বঙ্গীয় জনগণের সঙ্গে অতি প্রাচীনকালেই অস্ট্রিকভাষী জনগোষ্ঠীর সংযোগ ঘটেছিল এবং স্বল্প হলেও আধুনিক বাঙালী জন সৃষ্টিতে অস্ট্রিক উপদানের (গাদ্দী) অবদান রয়েছে। ১৪
দ্রাবিড় ভাষা পরিবারের ভৌগোলিক বিস্তার দেখলে আপাতত মনে হয়, বাংলা ভাষা ও তামিল ভাষা নিকটাত্মীয়ই, জেনেটিক বিশ্লেষণে প্রাপ্ত তথ্য বিরোধাভাসমূলক মনে হয় না। বাঙালির মাইটোকন্ড্রিয়াল ডিএনএ (এক্স -ক্রোমোজোম) বিশ্লেষণের পর এ বিষয়ে আরও তথ্য জানা যাবে। আশা করা যায় খুব শিগগিরই আমরা বাংলা ভাষা এবং আমাদের জাতিগত বৈশিষ্ট্যের শিকড় জানতে পারব।
1 Vargha-Khadem et al., 2005, p. 131
2 Simon Fisher, a neurogeneticist at the Max Planck Institute for Psycholinguistics in Nijmegen, the Netherlands, and his colleagues
3 Richard Huganir, the neurobiologist at Johns Hopkins University School of Medicine in Baltimore, Maryland
4 Gene, Brains and Language: An Epistemological Examination of How Genes Can Underlie Human Cognitive Behavior, Nathalie Gontier, American Psychological Association, Vol-12, 170-180
৫ ভাষা, সংস্কৃতি ও মানবস্বত্তা: একটা নৃবৈজ্ঞানিক আলাপচারিতা – বখতিয়ার আহমেদ
৬ 6 Ruhlen, M. (1991) A Guide to the Languages of the World (Standord Univ. Press, Stanford, CA)
7 Kamrul Hasan , Vinnochokh Language Issue.
8 Cavalli-Sforza, L.L., Menozzi, P., Piazza, A. & Mountain, J.L. (1988) Proc. Natl. Acad.Sci.USA 85, 6002-6006
9 Gene, peoples and languages, L.Luca Cavalli-Sforza, Department of Genetics, School of Medicine, Standford University, CA
10 Nei and Roychoudhury (1993)
11 Gazi NN, Tamang R. Sing VK, Ferdous A, Pathak AK, et al. (2013), Genetic Structure of Tibeto-Burman Populations of Bangladesh: Evaluating the Gene Flow along the Sides of Bay-of-Bangal
12 S. Alam, et al., Haplotype diversity of 17 Y-chromosomal STR loci in the Bangladeshi population, Forensic Sci. Int. Genet. (2009), doi:10.1016/j.fsigen.2009.05.005
১৩ গাদ্দি উপজাতি ((Gaddi Tribes) :- অত্যন্ত সৎ, শান্তি প্রিয়। এই উপজাতির মানুষেরা মূলত হিমাচল প্রদেশ এবং কিছু জম্মু ও কাশ্মীরে বসবাস করেন। এঁরা হিমাচল প্রদেশ এর মান্ডি, কাংড়া ও বিলাসপুর জেলায় বসবাস করেন। তবে সবচেয়ে বেশি বসবাস করেন কাংড়া জেলায়।
গাদ্দিথউপজাতি গন মূলত পশুপালক। তাদের মধ্যে ঋতুভিত্তিক পশুপালন বৃত্তি দেখা যায়। গ্রীষ্মকালে তারা উচ্চ হিমালয়ের চারনভূমি অ লে মেষ, ছাগল, ঘোড়া প্রভৃতি নিয়ে পরিব্রাজন করে। তবে এদের কিন্তু স্থায়ী বাসভূমি, গ্রাম রয়েছে। কিছু উপজাতি গন আবার পশুপালন ছাড়াও কৃষিকাজ, বয়ন, বাসন পত্র নির্মান ইত্যাদি কাজের সাথে ও যুক্ত। বর্তমানে তারা উপত্যকায় আপেল, চেষ্টনাট ইত্যাদি উৎপাদনের সাথে যুক্ত।
নৃতত্ববিদদের মতে এই উপজাতির উদ্ভব নিয়ে বিতর্ক আছে। যদিও অনেকেই মনে করেন এই উপজাতি গন এসেছে পাঞ্জাবের সমভূমি অ ল থেকে।
এই উপজাতির নারী পুরুষ উভয়েই রং বেরং এর পোষাক পড়তে ভালোবাসেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নৃত্য গীত এ তাঁরা পটু। তাঁরা বৈশাখী, লোহরী, পাত্রোরু, সাগরান্ড, শিবরাত্রি প্রভৃতি উৎসব পালন করে থাকেন।
১৪ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রখম খন্ড), প্রধান সম্পাদক: আনিসুজ্জামান, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩